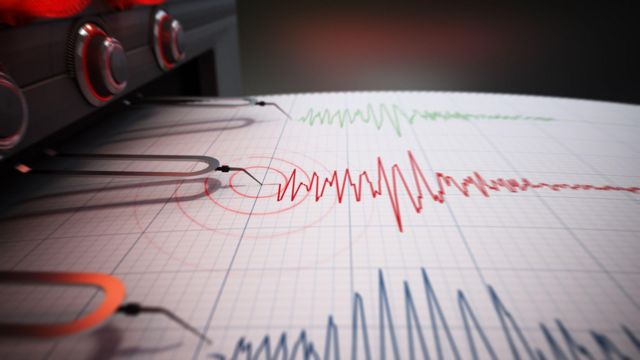ভূমিকম্প কি
ভূ -অভ্যন্তরে শিলায় পীড়নের জন্যে যে শক্তির সঞ্চয় ঘটে, সে শক্তি হঠাৎ মুক্তি পেলে ভূ-পৃষ্ঠ ক্ষণিকের জন্য কেঁপে ওঠে এবং ভূ-ত্বকের কিছু অংশ আন্দোলিত হয়; এইরূপ আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী কম্পনকে ভূমিকম্প বলে। সাধারণত কম্পন-তরঙ্গ থেকে যেই শক্তির সৃষ্টি হয়, তা ভূমিকম্পের মাধ্যমে প্রকাশ পায়। এই তরঙ্গ ভূ-গর্ভের কোন নির্দিষ্ট অঞ্চলে উৎপন্ন হয় এবং উৎসস্থল থেকে তা চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে।
ভূমিকম্প সাধারণত কয়েক সেকেন্ড থেকে ১/২ মিনিট স্থায়ী হয়। তবে খুবই কমসংখ্যক কিছু ভূমিকম্প ৮-১০ মিনিট পর্যন্ত স্থায়ী হয়। মাঝে মাঝে কম্পন এত দুর্বল হয় যে, তা অনুভবও করা যায় না। কিন্তু শক্তিশালী ও বিধ্বংসী ভূমিকম্পে ঘর-বাড়ি ও ধন-সম্পত্তির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয় এবং অসংখ্য প্রাণহানি ঘটে।
সাধারণ জ্ঞানে ভূমিকম্প শব্দটি দ্বারা যে কোন প্রকার ভূকম্পনজনিত ঘটনাকে বোঝায় – সেটা প্রাকৃতিক বা মনুষ্যসৃষ্ট যাই হোক না কেন। বেশিরভাগ ভূমিকম্পের কারণ হল ভূগর্ভে ফাটল ও স্তরচ্যুতি হওয়া; কিন্তু সেটা অন্যান্য কারণেও; যেমন: অগ্ন্যুৎপাত, ভূমিধস, খনিতে বিষ্ফোরণ বা ভূগর্ভস্থে নিউক্লিয়ার গবেষণায় ঘটানো আণবিক পরীক্ষা থেকেও হয়ে থাকতে পারে। ভূগর্ভে ভূমিকম্পের প্রাথমিক ফাটলকে বলে কেন্দ্র (ফোকাস) বা অধোকেন্দ্র (হাইপোসেন্টার) এবং অধোকেন্দ্র থেকে উল্লম্ব বরাবর ভূপৃষ্ঠে অবস্থিত কেন্দ্রটিকে উপকেন্দ্র (এপিসেন্টার) বলে।
আমাদের ভূ -পৃষ্ঠ অনেকগুলো প্লেট-এর সমন্বয়ে গঠিত। এই প্লেটগুলো একটি আরেকটির থেকে আলাদা থাকে ফল্ট বা ফাটল দ্বারা। এই প্লেটগুলোর নিচেই থাকে ভূ-অভ্যন্তরের সকল গলিত পদার্থ। কোনও প্রাকৃতিক কারণে এই গলিত পদার্থগুলোর স্থানচ্যুতি ঘটলে প্লেটগুলোরও কিছুটা স্থানচ্যুতি ঘটে। এ কারণে একটি প্লেটের কোনও অংশ অপর প্লেটের তলায় ঢুকে যায়, যার ফলে ভূমিতে কম্পন সৃষ্টি হয়। আর এই কম্পনই ভূমিকম্প রূপে আমাদের নিকট আবির্ভূত হয়।
গবেষকদের মতে, বিশ্বে বছরে গড়ে ছয় হাজার ভূমিকম্প হয়। এগুলোর বেশিরভাগই মৃদু, যা আমরা টের পাই না। সাধারণত তিন ধরনের ভূমিকম্প হয়- প্রচণ্ড, মাঝারি ও মৃদু।
আবার উৎসের গভীরতা অনুসারে ভূমিকম্পকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়- অগভীর, মধ্যবর্তী ও গভীর ভূমিকম্প। ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল ভূ-পৃষ্ঠের ৭০ কিলোমিটারের মধ্যে হলে অগভীর, ৭০ থেকে ৩০০ কিলোমিটারের মধ্যে হলে মধ্যবর্তী ও ৩০০ কিলোমিটারের নিচে হলে তাকে গভীর ভূমিকম্প হিসেবে চিহ্নিত করা হয়।
বাংলাদেশের আবহাওয়া অধিদপ্তর জানিয়েছে, গত সোমবার ২ অক্টোবর ২০২৩ সন্ধ্যা ৬.৪৫ মিনিটে ৫.২ মাত্রার একটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে।এর কেন্দ্রস্থল ঢাকার ভূমিকম্প পর্যবেক্ষণ ও গবেষণা কেন্দ্র থেকে ২৩৬ কিলোমিটার দূরে। এটি একটি মাঝারি মাত্রার ভূমিকম্প।বাংলাদেশ ছাড়াও এই ভূমিকম্প নেপাল, ভারত, ভুটান এবং চীনে অনুভূত হয়েছে।
ভারতের ন্যাশনাল সেন্টার ফর সিসমোলজির তথ্য অনুযায়ী, ভারতের মেঘালয়ের উত্তরে গারো পাহাড় এলাকায় পাঁচ দশমিক দুই মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে।ভূমিকম্পটির গভীরতা ছিল ১০ কিলোমিটার। ভারতের স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬.১৫ মিনিটে এই ভূমিকম্প অনুভূত হয়।উৎপত্তিস্থল ছাড়াও ভারতের পশ্চিমবঙ্গ এবং আসামেও কম্পন অনুভূত হয়েছে।
গত পাঁচ মাসে যত ভূমিকম্প
এরআগে গত সেপ্টেম্বরে রাজধানী ঢাকাসহ দেশের বিভিন্ন এলাকায় ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে বলে জানা যায়।
গত ০৯ই সেপ্টেম্বর সিলেট ও এর আশপাশের এলাকায় ৪.৫ মাত্রার একটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এর উৎপত্তিস্থল ছিল ভারতের আসামে।
গত ১৭ই সেপ্টেম্বর রবিবার দুপুরে ৪ দশমিক ২ মাত্রার একটি ভূমিকম্প অনুভূত হয়। এর উৎপত্তিস্থল ছিলো ঢাকা থেকে ৬০ কিলোমিটার দুরে টাঙ্গাইলের একটি এলাকায়।
এর আগে চলতি বছরের মে মাস থেকে শুরু করে অগাস্ট পর্যন্ত চার মাসে মোট তিন বার ছোট থেকে মাঝারি আকারের ভূমিকম্প অনুভূত হয়। যার মধ্যে প্রায় প্রতিটির উৎপত্তিস্থল ছিল দেশের সীমানার ভেতর বা আশেপাশে।
১৪ই অগাস্ট রাত ৮টা ৪৯ মিনিটের দিকে একটি ভূমিকম্প অনুভূত হয় রাজধানীসহ দেশের বেশিরভাগ এলাকায়।
মার্কিন ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস-এর তথ্য অনুযায়ী, এই ভূমিকম্পটির মাত্রা রিখটার স্কেলে ছিল ৫.৫, যা মাঝারি মাত্রার একটি ভূমিকম্প। আর এর উৎপত্তিস্থল ছিল বাংলাদেশ-ভারত সীমান্তের সিলেটের কানাইঘাট এলাকায়। গভীরতা ছিল মাত্র ১০ কিলোমিটার।
এর আগে, গত ১৬ই জুন রাজধানীসহ সারা দেশে ৪.৫ মাত্রার মৃদু ভূমিকম্প হয়। এর উৎপত্তিস্থল ছিল সিলেটের গোলাপগঞ্জ।
আর চলতি বছরের মে মাসের পাঁচ তারিখে আরেকটি ভূমিকম্প হয়েছে ঢাকা ও এর আশেপাশের এলাকায়।
যুক্তরাষ্ট্রের ভূ-তাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা ইউএসজিএস এর হিসেব অনুযায়ী, এই ভূমিকম্পের মাত্রা ছিল ৪.৩। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থল ছিল ঢাকার কাছে বিক্রমপুরের দোহার থেকে প্রায় ১৪ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে। এটিরও গভীরতা ছিল মাত্র ১০ কিলোমিটার।
ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞরা তখন বলেছিলেন, বার্মিজ প্লেট ও ইন্ডিয়ান প্লেটের পরস্পরমুখী গতির কারণেই এ ধরণের ভূমিকম্প হচ্ছে।
তারা জানান, এই দুটি প্লেটের সংযোগস্থলে প্রচুর পরিমাণে শক্তি জমে রয়েছে যেগুলো বের হয়ে আসার পথ খুঁজছে। আর সে কারণেই ঘন ঘন এমন ভূমিকম্প অনুভূত হচ্ছে।
ভূমিকম্প হচ্ছে ভূমির কম্পন। ভূ অভ্যন্তরে যখন একটি শিলা অন্য একটি শিলার উপরে উঠে আসে তখন ভূমি কম্পন হয়। পৃথিবীপৃষ্ঠের অংশবিশেষের হঠাৎ অবস্থান পরিবর্তন বা আন্দোলনই ভূমিকম্পন।

বাংলাদেশের ভূমিকম্প বলতে বাংলাদেশ ও তৎসংলগ্ন এলাকার ভূমিকম্পকে বোঝায়। কারণ বাংলাদেশ আসলে ভারত ও মিয়ানমারের ভূঅভ্যন্তরের দুটি ভূচ্যুতিরেখার (faultline) প্রভাবে আন্দোলিত হয়। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ও ভারত ইউরেশীয় এবং মিয়ানমার বার্মার ভূগাঠনিক পাতের মধ্যে অবস্থান করছে। ভারতীয় এবং ইউরেশীয় পাত দুটি (১৯৩৪ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে) দীর্ঘদিন যাবৎ হিমালয়ের পাদদেশে আটকা পড়ে আছে, অপেক্ষা করছে বড় ধরনের নড়াচড়ার,অর্থাৎ বড় ধরনের ভূ-কম্পনের। বাংলাদেশে ৮টি ভূতাত্ত্বিক চ্যুতি এলাকা বা ফল্ট জোন সচল অবস্থায় রয়েছে, যথা: বগুড়া চ্যুতি এলাকা, রাজশাহীর তানোর চ্যুতি এলাকা, ত্রিপুরা চ্যুতি এলাকা, সীতাকুণ্ড টেকনাফ চ্যুতি এলাকা, হালুয়াঘাট চ্যুতির ডাওকী চ্যুতি এলাকা, ডুবরি চ্যুতি এলাকা, চট্টগ্রাম চ্যুতি এলাকা, সিলেটের শাহজীবাজার চ্যুতি এলাকা (আংশিক-ডাওকি চ্যুতি) এবং রাঙামাটির বরকলে রাঙামাটি চ্যুতি এলাকা।
প্রাকৃতিকভাবেই কার্বন চক্রের প্রভাবে ভূমিকম্প হয়ে থাকে, বাংলাদেশেও তার ব্যতিক্রম হয় না। এদেশের ভিতরে ও পার্শ্ববর্তী এলাকার বিগত প্রায় ২৫০ বছরের ভূমিকম্পের নথিভুক্ত তালিকা পাওয়া যায়। এ তালিকা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ১৯০০ খ্রিষ্টাব্দের পর থেকে ২০০৪ পর্যন্ত বাংলাদেশে সংঘটিত হয়েছে ১০০’রও বেশি ভূমিকম্প; তন্মধ্যে ৬৫টিরও বেশি ঘটেছে ১৯৬০ খ্রিষ্টাব্দের পরে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিগত ৩০ বছরে (পরিপ্রেক্ষিত ২০০৪) ভূমিকম্প সংঘটনের মাত্রা বেড়েছে।
ভূমিকম্প হয় কত বছর পর পর
বিজ্ঞানীরা তাদের গবেষণায় দেখেছেন সাবডাকশন জোনে বড় আকারের দুটো ভূমিকম্পের মাঝখানে সময়ের ব্যবধান হচ্ছে ৮০০ থেকে ৯০০ বছর।
ময়নামতি পাহাড়ে বৌদ্ধ বিহারের যে স্থাপনা আছে, ওই এলাকা থেকে লোকজন অভিবাসন করে চলে গিয়েছিল ৮০০ থেকে ১,০০০ বছর আগে। তাদের ওই অভিবাসনের সঙ্গে ভূমিকম্পের সম্পর্ক ছিল।
“তাহলে আমরা ধরে নিতে পারি এখানে যে শক্তি সঞ্চিত ছিল সেটা ৮০০ বা ১০০০ বছর আগে ছেড়ে দিয়েছে এবং নতুন করে শক্তি সঞ্চিত হচ্ছে,” বলছিলেন ঢাকায় ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ হুমায়ুন আখতার।
তাই আরেকটা বড় মাপের ভূমিকম্পের আশংকা আছেও বলে সতর্ক করে দিয়েছেন তিনি।
বাংলাদেশে বড় ভূমিকম্পের ইতিহাস
বাংলাদেশের সিলেট, চট্টগ্রাম এবং ঢাকায় ১৫৪৮, ১৬৪২, ১৬৬৩, ১৭৬২, ১৭৬৫, ১৮১২, ১৮৬৫, ১৮৬৯ সালে ভূমিকম্প হওয়ার ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায়। তবে এসবের মাত্রা কত ছিল তা জানা যায় না।এছাড়া ১৮২২ ও ১৮১৮ সালে সিলেট ও শ্রীমঙ্গলে ৭.৫ ও ৭.৬ মাত্রার ভূমিকম্প হয়। অবশ্য এর ক্ষয়ক্ষতির তেমন বর্ণনা পাওয়া যায় না।গবেষকদের মতে বাংলাদেশে গত ১২০-২৫ বছরে মাঝারি ও বড় মাত্রার প্রায় শতাধিক ভূকম্প অনুভূত হয়েছে।
তবে এসবের মধ্যে রিখটার স্কেলে সাত বা তার চেয়ে বড় মাত্রার ভূমিকম্পের সংখ্যা খুব বেশি নয়। যদিও বাংলাদেশ ভূমিকম্প-প্রবণ অঞ্চলে অবস্থিত এবং এর নিচে যে পরিমাণ শক্তি জমা হয়ে আছে তা বের হলে বাংলাদেশে বেশ বড় ধরণের ভূমিকম্পের আশঙ্কা রয়েছে বলে বিশেষজ্ঞরা ধারণা করেন।
বাংলাদেশ ভূমিকম্পের বড় ঝুঁকিতে
ভূতত্ত্ব বিশেষজ্ঞরা বলছেন, বাংলাদেশের সিলেট থেকে চট্টগ্রাম অঞ্চলে কয়েকটি প্লেট থাকার কারণে এসব এলাকা ভূমিকম্পের বড় ঝুঁকিতে রয়েছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভু-তত্ত্ব বিভাগের সাবেক অধ্যাপক সৈয়দ হুমায়ুন আখতার বলছেন, ‘’উত্তরে তিব্বত সাব-প্লেট, ইন্ডিয়ান প্লেট এবং দক্ষিণে বার্মা সাব-প্লেটের সংযোগস্থলে বাংলাদেশের অবস্থান। ফলে সিলেট-সুনামগঞ্জ হয়ে, কিশোরগঞ্জ চট্টগ্রাম হয়ে একেবারে দক্ষিণ সুমাত্রা পর্যন্ত চলে গেছে।‘’
কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় দুই যুগ ধরে এ নিয়ে গবেষণা করেছে।সেখানে দেখা গেছে, ইন্ডিয়া প্লেট ও বার্মা প্লেটের সংযোগস্থলে দীর্ঘসময় ধরে কোন ভূমিকম্পের শক্তি বের হয়নি। ফলে সেখানে ৪০০ থেকে হাজার বছর ধরে শক্তি জমা হয়ে রয়েছে।
ইন্ডিয়া প্লেট পূর্ব দিকে বার্মা প্লেটের নীচে তলিয়ে যাচ্ছে আর বার্মা প্লেট পশ্চিম দিকে অগ্রসর হচ্ছে। ফলে সেখানে যে পরিমাণ শক্তি জমা হচ্ছে, তাতে আট মাত্রার অধিক ভূমিকম্প হতে পারে।
অধ্যাপক সৈয়দ হুমায়ুন আখতার বলছেন, ”এটা যেমন একবারে হতে পারে, আবার কয়েকবারেও হতে পারে। তবে যে কোনো সময় বড় ধরনের ভূমিকম্প হতে পারে বলে তারা আশঙ্কা করছেন। সাধারণত এ ধরনের ক্ষেত্রে সাত বা আট মাত্রার ভূমিকম্প হয়ে থাকে। কিন্তু কবে বা কখন সেটা হবে, তা এখনো বিজ্ঞানীদের এখনো ধারণা নেই।”
সানফ্রানসিসকো বা দক্ষিণ আমেরিকার ভূমিকম্পের সঙ্গে এর মিল রয়েছে।সুনামগঞ্জ, জাফলং অংশে ডাউকি ফল্টের পূর্বপ্রান্তেও ভূমিকম্পের ঝুঁকি রয়েছে বলে বিজ্ঞানীরা আশঙ্কা করছেন।এসব ফল্টে ভূমিকম্প হলে ঢাকাসহ সারা বাংলাদেশে বড় ধরনের ক্ষয়ক্ষতির আশঙ্কা বা বিপদের মাত্রা অনেক বেশি বলে তিনি আশঙ্কা করছেন।
বাংলাদেশে সর্বশেষ ১৮২২ এবং ১৯১৮ সালে মধুপুর ফল্টে বড় ভূমিকম্প হয়েছিল। ১৮৮৫ সালে ঢাকার কাছে মানিকগঞ্জে ৭.৫ মাত্রার একটি ভূমিকম্পের ইতিহাস রয়েছে।
প্রাকৃতিক যে সকল দুর্যোগ সংঘঠিত হয়ে থাকে সেগুলোর মধ্যে বন্যা, ঘূর্ণিঝড়, সাইক্লোন, জলোচ্ছাস, নদীভাঙ্গন ইত্যাদি সম্পর্কে আমাদের অভিজ্ঞতা থাকলেও ভূমিকম্প সম্পর্কিত তিক্ত জ্ঞান নেই বললেই চলে৷ প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, জাতিসংঘ বলছে পৃথিবীর সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ২০টি শহরের মধ্যে ঢাকা অন্যতম৷
এছাড়া বাংলাদেশ পৃথিবীর ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল এ অবস্থিত বিধায় প্রাচীনকাল থেকে এই দেশে মাঝে মাঝে ভূমিকম্প সংঘটিত হয়৷ উপরন্তু হিমালয় রেঞ্জ হচ্ছে এশিয়ার মধ্যে সবচেয়ে ভূমিকম্পপ্রবণ অঞ্চল৷ যদিও সৌভাগ্যক্রমে বাংলাদেশের জনগণকে শক্তিশালী ভূমিকম্পের তিক্ত স্বাধ গ্রহণ করতে হয়নি তথাপি গত দুই শতাব্দির ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বাংলাদেশের উত্তর, উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে, দক্ষিণ-পূর্ব অঞ্চলে ভূমিকম্পের বড় ধরনের আশংকাআছে৷
উদাহরণ স্বরূপ ১৮৯৭ সালের ১২ই জুন মেঘালয়ের শিলং এর কাছে যে মারাত্বক ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়েছিল তার ফলে বাংলাদেশের ঢাকা, সিলেট ও ময়মনসিংহসহ অনেক শহরের দালান কোঠা ভেঙ্গে পড়ে এবং অনেক লোক প্রাণ হারায়৷
বিগত ২১শে নভেম্বর ১৯৯৭ সালে চট্রগ্রাম ও তৎসংলগ্ন এলাকায় এক প্রচন্ড ভূমিকম্প আঘাত হানে এবং অনূরূপভাবে ১৯৯৯ সালের জুলাই-আগষ্ট মাসে মহেষখালি ও পার্শ্ববর্তী এলাকায় প্রায় চার দফা ভূমিকম্প সংঘটিত হয় যার ফলে এই সব এলাকায় বেশ কিছু লোক মারা যায় এবং বাড়ি ঘর ধ্বংস প্রাপ্ত হয়৷
এছাড়া রেকর্ড অনুযায়ী ১৯৯৮ সালে ১০বার, ১৯৯৯ সালে ২১বার, ২০০০ সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত মোট ১৪বার ভূ কম্পন হয়েছে যা সুস্পষ্টভাবে ইহাই ইঙ্গিত করে যে ভূমিকম্প যে কোন মুহূর্তে বাংলাদেশের জন্য অভিশাপের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে৷ ইতিহাস থেকে জানা যায় ভূমিকম্পের কারণে নদ নদীর গতি পরিবর্তন হয়ে গেছে বা পাহাড় ও টিলার সৃষ্টি হয়েছে৷ ব্রহ্মপুত্র নদীর গতি পরিবর্তন, মধুপুরের গড় সৃষ্টি ভূমিকম্পের কারণেই হয়েছে বলে ভূ-তত্ত¡বিদরা ও ইতিহাসবিদরা মনে করেন৷ উপরন্তু মাত্র ৫৫ হাজার বর্গমাইল এলাকায় ১৬ কোটি লোকের বসবাস, অপরিকল্পিত নগরায়ন এবং ঝুঁকিপূর্ণ অননুমোদিত ভবন সম্ভাব্য ভুমিকম্পের ক্ষয়ক্ষতিকে আরও ভয়াবহ করে তুলবে৷ এহেন পরিস্থিতিতে ভূমিকম্প সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান অর্জন ও প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি গ্রহণ তথা সচেতন হওয়া একান্ত প্রয়োজন৷
ভূমিকম্প ঝুঁকি মোকাবেলায় করণীয়
ভূমিকম্প সংক্রান্ত ঝুঁকিসমূহ চিহ্তিকরণ (কোথায় কোথায় ঝুঁকি, ভবন, ভূমি, অকুপেন্সী টাইপ ইত্যাদি), ঝুঁকি মূল্যায়ণ (কী ধরনের ক্ষয়ক্ষতি হতে পারে)
· জাতীয়ভাবে ভূমিকম্পে ঝুঁকি হ্রাসকরণে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ এবং প্রয়োজনে আইন-বিধি প্রণয়ন ও স্থানীয় প্রতিনিধি এবং জনসাধারণকে সম্পৃক্তকরণ৷
· ঝুঁকি হ্রাসকরণে আন্তর্জাতিক নতুন নতুন ধারণা ও গবেষণার সাথে সামঞ্জস্য রেখে জাতীয় নীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন৷
· ঝুঁকি হ্রাসকরণে সরকারি-বেসরকারি যৌথভাবে উদ্যোগ গ্রহণের মাধ্যমে সরকারি, বেসরকারি সকল ভবন, শিল্প কারখানাসহ সকল ক্ষেত্রে ঝুঁকি হ্রাসকরণে ব্যবস্থা গ্রহণ৷
· দুর্যোগ-দুর্ঘটনায় কার্যকর সাড়া প্রদানের লক্ষ্যে ফায়ার সার্ভিসসহ জরুরী সাড়া প্রদানকারী বাহিনীসমূহকে আধুনিক যন্ত্রপাতি ও প্রশিক্ষিত জনবল দিয়ে প্রস্তুতকরণ এবং যন্ত্রপাতি বিকেন্দ্রীয়করণ৷
· দুর্যোগ-দুর্ঘটনা পরবর্তী পুনর্বাসন ও পুনর্গঠনের ক্ষেত্রে “Build Back Better” অর্থ্যাৎ আরো দুর্যোগ সহনীয়ভাবে পুনর্গঠন কার্যক্রম সম্পন্ন করণ৷
· প্রত্যেকটি সাড়াদানকারী প্রতিষ্ঠানের জন্য “Contingency Plan” প্রস্তুতকরণ ও এতদসংক্রান্ত মহড়া পরিচালনা করা৷
· শিল্প-কারখানা ও বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানসহ সকল প্রতিষ্ঠানের জন্য “Business Continuity Plan” প্রস্তুতকরণ ও এতদসংক্রান্ত মহড়া পরিচালনা করা৷
· সকল প্রতিষ্ঠানে আপদকালীন সময়ের জন্য মহড়া পরিচালনা করা এবং এতদসংক্রান্ত জাতীয় নীতিমালা/আইন প্রণয়ন করা৷
· বড় ধরনের দুর্যোগে সকল বিভাগের মধ্যে সমন্বিত কার্যক্রমের জন্য “Incident Command System” চালু করা৷
· দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে লজিস্টিক মালামালসমূহের যথাযথ সমন্বয়ের জন্য প্রয়োজনীয় ডাটাবেজসহ “Emergency Operation Center” চালু করা৷
· নিরাপদ ভবন নির্মাণের ক্ষেত্রে Bangladesh Natiional Building Code (BNBC) বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা এবং এতদলক্ষ্যে ভবন নির্মাণ তদারকি কর্তৃপক্ষ গঠন করা যেতে পারে৷
· বিদ্যমান ঝুঁকিপূর্ণ স্থাপনা চিহ্নিতকরণ এবং স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ; প্রয়োজনে ভবন অপসারণ অথবা ব্যাংক হতে ঝৃণ প্রদানের মাধ্যমে রেট্রোফিটিং বা নতুন ভবন নির্মাণ করা৷
· সিসমিক জোনেসন ম্যাপ প্রণয়ন ও তদনুযায়ী ভবন নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন করা৷
· দুর্যোগের পূর্বেই আশ্রয়স্থলের জন্য পার্ক বা খোলা জায়গা জোন অনুযায়ী চিহ্নিতকরণ এবং এতদসংক্রান্ত মহড়া পরিচালনা করা৷
· বড় ধরনের দুর্যোগের জন্য পূর্বেই খাবার, প্রয়োজনীয় মালামাল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির মজুদ রাখা এবং বিকেন্দ্রীকরণ করা৷
· সিভিল মিলিটারি কোঅপারেশনের জন্য প্রয়োজনীয় আইন-নীতিমালা প্রণয়ন ও মহড়া পরিচালনা করা৷
· সকল ক্ষেত্রে আইনের বাস্তবায়ন নিশ্চিতকরণ৷
· সরু রাস্তা ও সরু ভবনের জন্য স্বল্পমেয়াদী, মধ্যমেয়াদী ও দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনার মাধ্যমে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও প্রয়োজনে এ বিষয়ে বিনিয়োগের জন্য ব্যাংক লোন প্রদান করা৷
· দুর্যোগ প্রতিরোধে করণীয় বিষয়ে পাঠ্যপুস্তকে অন্তর্ভূক্ত করা৷
· দুর্যোগ প্রকৌশল সম্পর্কে উচ্চ শিক্ষার মাধ্যমে এক্ষেত্রে পেশাজীবি প্রস্তুত করা৷
· প্রকৌশলী, রাজমিস্ত্রী ও ভবন সংক্রান্ত পেশাজীবীদের ভূমিকম্প প্রতিরোধমূলক ডিজাইন সংক্রান্ত প্রশিক্ষণ প্রদান৷
· দুর্যোগের পর তথ্য প্রযুক্তির মাধ্যমে ক্ষয়ক্ষতি নিরুপনের জন্য প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ প্রদান ও প্রস্তুতি গ্রহণ৷
· আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় আইন-বিধিমালা প্রণয়ন ও আপডেট করা৷
· আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গ্রহণের জন্য বিমানবন্দর প্রস্তুত করা এবং বিকল্প বিমানবন্দর চিহ্নিত ও প্রস্তুত রাখা৷
· মোবাইল হসপিটাল এবং ব্লাড ব্যাংকের প্রস্ততি গ্রহণ করা৷
· গ্যাস ও বিদ্যুৎ লাইনের জন্য অটো শাট ডাউন সিস্টেম স্থাপন করা যেন আকস্মিক ভূমিকম্পে লাইন স্বয়ংক্রিয়ভাবে বন্ধ হয়ে যায়৷
ভূমিকম্পের পূর্বাভাস দেওয়া কঠিন তাই ভূমিকম্প মোকাবেলায় প্রতিরোধ ব্যবস্থা ও সচেতনতার বিকল্প নেই৷ একমাত্র প্রয়োজনীয় প্রস্তুতিই পারে ভূমিকম্প এর ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমিয়ে ভূমিকম্প সহনশীল দেশ গড়তে৷
তথ্যসূত্র: উইকিপিডিয়া,বিবিসি বাংলা, ডয়েচ ভেলে