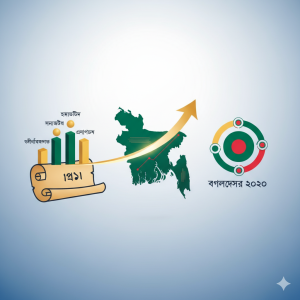বাংলাদেশ বর্তমানে একটি গভীর পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পথ অতিক্রম করছে- একটি গবেষণা ধর্মী বিশ্লেষণ
রুহুল কুদ্দুস টিটো
I. বিশ্লেষণাত্মক কাঠামো
A. প্রধান বিশ্লেষণমূলক পর্যবেক্ষণ (গতির সংশ্লেষণ)বাংলাদেশ বর্তমানে একটি গভীর পরিবর্তনশীল রাজনৈতিক পথ অতিক্রম করছে। ৫৪ বছর পর রাষ্ট্রটির গতিপথ কোনো সরল গণতান্ত্রিক বা সরাসরি ধর্মতান্ত্রিক রূপান্তরের দিকে নয়, বরং এটি একটি তীব্র প্রতিযোগিতামূলক, মিশ্র রাষ্ট্রীয় পরিচিতি (Contested Hybridity)-র মাধ্যমে অগ্রসর হচ্ছে। দীর্ঘদিনের জেঁকে বসা কর্তৃত্ববাদী হাইব্রিড শাসন থেকে বেরিয়ে আসার পর, রাষ্ট্রটি এখন সাংবিধানিক ও আদর্শিক অস্থিরতার মুখোমুখি । এই গতিপথ একটি সরাসরি ধর্মতান্ত্রিক রাষ্ট্রে রূপান্তরের চেয়ে বরং ইসলামপন্থী রাজনৈতিক সমঝোতার দিকে বিপজ্জনকভাবে দ্রুত অগ্রসর হওয়ার ইঙ্গিত দেয়, যেখানে অপেক্ষাকৃত কঠোর ইসলামপন্থী, অ-নির্বাচনী গোষ্ঠীগুলো নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে নজিরবিহীন প্রভাব বিস্তার করছে ।
এই পরিবর্তনের মূল অনুঘটক ছিল ২০২৪ সালের ছাত্রনেতৃত্বাধীন গণঅভ্যুত্থান। এই অভ্যুত্থান প্রাথমিকভাবে গণতান্ত্রিক ঘাটতি এবং প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতির বিরুদ্ধে জনরোষ হিসেবে শুরু হলেও , সৃষ্ট ক্ষমতা শূন্যতা (power vacuum) পূর্বে দমন করে রাখা আদর্শবাদী ইসলামপন্থী অভিনেতাদের জন্য একটি তাৎক্ষণিক এবং গুরুতর সুযোগ সৃষ্টি করে। এর ফলে মূল রাজনৈতিক প্রতিযোগিতা ‘গণতন্ত্র বনাম স্বৈরতন্ত্র’ থেকে সরে গিয়ে ‘ধর্মনিরপেক্ষতা বনাম ইসলামবাদ’-এর দিকে মোড় নেয়। বর্তমান সময়ে রাষ্ট্রের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঝুঁকি হলো অন্তর্বর্তী সরকারের পক্ষ থেকে হার্ডলাইন ইসলামপন্থী গোষ্ঠীগুলোকে (যেমন, হেফাজত, হিজবুত তাহরীর) রাজনৈতিকভাবে স্থান দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা, যা সাংবিধানিক ধর্মনিরপেক্ষতার মূলনীতিকে স্থায়ীভাবে ক্ষুণ্ন করতে পারে এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের দুর্বলতা বাড়িয়ে দিতে পারে ।
B. সাংবিধানিক পরিচয়ের সংজ্ঞা: দ্বৈততা ও অস্থিরতাবাংলাদেশের সাংবিধানিক পরিচয়ের ভিত্তি জন্মলগ্ন থেকেই দ্বৈততায় পূর্ণ এবং ক্রমাগত প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ। ১৯৭২ সালের মূল সংবিধান রাষ্ট্রকে চারটি মৌলিক আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠা করেছিল: জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র এবং ধর্মনিরপেক্ষতা । তবে, এই পরিচয় পরবর্তীকালে সাংবিধানিকভাবে খণ্ডিত হয়েছে। ২০১১ সালের পঞ্চদশ সংশোধনী ধর্মনিরপেক্ষতাকে (অনুচ্ছেদ ১২) সাংবিধানিক নীতি হিসেবে পুনরুদ্ধার করলেও, ১৯৮৮ সালের সামরিক শাসনামলে যুক্ত হওয়া ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ঘোষণা করা অনুচ্ছেদ ২ক-কে বহাল রাখে । এই দ্বৈততা রাষ্ট্রের মৌলিক আদর্শিক স্থিতিশীলতাকে চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছে।
এই প্রতিবেদনটি একটি ভূ-রাজনৈতিক কাঠামোর অধীনে বিশ্লেষণ করে দেখায় যে, প্রাতিষ্ঠানিক ভঙ্গুরতা (২০২৪-পরবর্তী রাজনৈতিক শূন্যতা), আদর্শিক প্রতিযোগিতা এবং বাহ্যিক/সামাজিক প্রভাব (যেমন, জনগণের উচ্চ ধর্মীয় মনোভাব এবং বৈশ্বিক ইসলামবাদ) কীভাবে বাংলাদেশের বর্তমান গতিপথকে প্রভাবিত করছে ।
II. বিতর্কের ভিত্তি: সাংবিধানিক ও ঐতিহাসিক বিবর্তন (১৯৭১–২০১১)
A. ধর্মনিরপেক্ষ জন্ম এবং দ্রুত ক্ষয় (১৯৭২–১৯৭৫)স্বাধীনতার পর, ১৯৭২ সালের সংবিধান স্পষ্টতই পাকিস্তানের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের পরিচিতি থেকে দেশকে আলাদা করতে চেয়েছিল । ধর্মনিরপেক্ষতাকে মূলত সাম্প্রদায়িকতা-বিরোধী নীতি এবং রাষ্ট্র কর্তৃক কোনো বিশেষ ধর্মকে রাজনৈতিক মর্যাদা বা সুযোগ-সুবিধা প্রদান না করার নীতি হিসেবে সংজ্ঞায়িত করা হয়েছিল । কিন্তু, প্রতিষ্ঠাতা নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের শাসনামলে ১৯৭৫ সালের চতুর্থ সংশোধনীর মাধ্যমে সংসদীয় গণতন্ত্র রাতারাতি একদলীয় কর্তৃত্ববাদী শাসনের দ্বারা প্রতিস্থাপিত হয়, যা পরবর্তীকালে সাংবিধানিক কারসাজির ভিত্তি তৈরি করে ।
B. ধর্মীয় পরিচিতির প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ (১৯৭৫–১৯৯০)
১৯৭৫ সালের ক্যু-এর পরে বিভিন্ন সামরিক শাসন আমলে, রাষ্ট্রের মৌলিক আদর্শ (বিশেষত সমাজতন্ত্র, ধর্মনিরপেক্ষতা, এবং জাতীয়তাবাদ) ক্রমান্বয়ে বাতিল বা উপেক্ষা করা হয় । ১৯৭২ সালে নিষিদ্ধ হওয়া ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে ১৯৭৬ সালে পুনরায় রাজনীতি করার অনুমতি দেওয়া হয় । এরশাদ সরকারের আমলে ১৯৮৮ সালের অষ্টম সংশোধনীর মাধ্যমে ইসলামকে আনুষ্ঠানিকভাবে রাষ্ট্রধর্ম (অনুচ্ছেদ ২ক) হিসেবে ঘোষণা করা হয় । এটি ছিল একটি যুগান্তকারী মুহূর্ত যা রাষ্ট্রের আত্ম-সংজ্ঞাকে মৌলিকভাবে পরিবর্তন করে এবং ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দাবিগুলোর বৈধতা দেয়।
C. আওয়ামী লীগের মোডাস ভিভেনডি বা আপোষমূলক অবস্থান (২০০৯–২০২৪)
২০১১ সালের পঞ্চদশ সংশোধনী রাজনৈতিকভাবে একটি বিতর্কিত পদক্ষেপ ছিল। এটি রাষ্ট্রের মূলনীতি হিসেবে ধর্মনিরপেক্ষতা এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠাতা নীতিগুলো পুনরুদ্ধার করে । কিন্তু একইসাথে, রাজনৈতিক বাস্তবতার বিবেচনায় সরকার অনুচ্ছেদ ২ক (রাষ্ট্রধর্ম) বহাল রাখে ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষণে দেখা যায় যে, ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পূর্ণরূপে বাদ দিতে অস্বীকৃতি জানালেও অনুচ্ছেদ ২ক বহাল রাখার মাধ্যমে আওয়ামী লীগ (AL) এক ধরনের আপোষমূলক নীতি (modus vivendi) গ্রহণ করে । এর মাধ্যমে দলটি একদিকে ধর্মনিরপেক্ষ সুশীল সমাজের সমর্থন নিশ্চিত করে, অন্যদিকে গভীরভাবে রক্ষণশীল, ধর্মীয় ভোটারদের বিচ্ছিন্ন হওয়া এড়িয়ে যায় । এই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত সাংবিধানিক দ্বৈততা মৌলিক কাঠামোটির স্থিতিশীলতা হ্রাস করে। সংবিধানকে রাষ্ট্রের একটি দৃঢ় আদর্শিক নোঙর হিসেবে ব্যবহার না করে, এটি কার্যত রাজনৈতিক টিকে থাকার জন্য নমনীয় হাতিয়ারে পরিণত হয়।
এই সময়ের সাংবিধানিক যাত্রাপথের সারসংক্ষেপ নিম্নোক্ত সারণিতে তুলে ধরা হলো:
Table I: সাংবিধানিক গতিপথ: ধর্মনিরপেক্ষতা ও রাষ্ট্রধর্ম
| সময়কাল | প্রধান সাংবিধানিক পরিবর্তন/সংশোধনী | মৌলিক নীতিসমূহ (আদর্শিক অবস্থান) | সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ |
| ১৯৭২ | মূল সংবিধান | ধর্মনিরপেক্ষতা, জাতীয়তাবাদ, সমাজতন্ত্র, গণতন্ত্র | অনুচ্ছেদ ১২ (ধর্মনিরপেক্ষতা) |
| ১৯৭৬-১৯৭৯ | সামরিক আইন ঘোষণা | ধর্মনিরপেক্ষতা অপসারণ; ধর্মভিত্তিক দলগুলোর জন্য অনুমতি | অনুচ্ছেদ ১২ বাতিল (কার্যত) |
| ১৯৮৮ | অষ্টম সংশোধনী | ইসলামকে রাষ্ট্রধর্ম ঘোষণা | অনুচ্ছেদ ২ক সন্নিবেশিত |
| ২০১১ | পঞ্চদশ সংশোধনী | ধর্মনিরপেক্ষতা পুনরুদ্ধার (একটি নির্দেশক নীতি হিসেবে), তবে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে ইসলাম বহাল | অনুচ্ছেদ ২ক এবং অনুচ্ছেদ ১২ উভয়ই বহাল |
III. গণতান্ত্রিক ঘাটতি: প্রাক-২০২৪ কর্তৃত্ববাদী প্রবণতা
A. গণতান্ত্রিক পশ্চাদপসরণ এবং প্রাতিষ্ঠানিক পতন
বাংলাদেশের রাজনৈতিক গতিপথ ক্রমাগত গণতান্ত্রিক পশ্চাদপসরণের মধ্য দিয়ে গেছে, বিশেষত ২০১৪ এবং ২০১৮ সালের অ-অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের পর দেশটি একটি “প্রকৃত মিশ্র শাসন” (truly hybrid regime) এবং পরে স্বৈরতন্ত্রের দিকে ধাবিত হয় । বৈশ্বিক সূচকগুলো রাজনৈতিক অধিকার, নাগরিক স্বাধীনতা, প্রতিনিধিত্ব, এবং অংশগ্রহণের ক্ষেত্রে এই পতন নিশ্চিত করে । যেমন, ২০২৪ সালের আইডিয়ার ডেমোক্রেসি ট্র্যাকারে প্রতিনিধিত্ব ক্যাটাগরিতে দেশটির বৈশ্বিক অবস্থান ছিল ১৭৩টির মধ্যে ১৫১তম, যা রাজনৈতিক অন্তর্ভুক্তির গুরুতর অভাব তুলে ধরে ।
আওয়ামী লীগ সরকার ক্ষমতা ধরে রাখতে মারাত্মক মানবাধিকার লঙ্ঘন, যার মধ্যে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড এবং জোরপূর্বক গুম অন্তর্ভুক্ত, অবলম্বন করে । সমালোচক, সাংবাদিক, এমনকি অপ্রাপ্তবয়স্কদের নীরব করতে ২০১৮ সালের ডিজিটাল নিরাপত্তা আইনের (DSA) মতো নিপীড়নমূলক আইন ব্যবহার করা হয়েছিল । ২০১৮ সালের অক্টোবর থেকে ২০২২ সালের আগস্ট পর্যন্ত অন্তত ২,৮৮৯ জনকে ডিএসএ-এর অধীনে অভিযুক্ত করা হয়েছিল ।
B. বাংলাদেশ প্যারাডক্স: সুশাসনের ব্যর্থতার মধ্যে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি
বাংলাদেশ সম্প্রতি চিত্তাকর্ষক আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন সাধন করেছে। দেশটি এখন ২০২৬ সালের মধ্যে স্বল্পোন্নত দেশের (LDC) মর্যাদা থেকে উত্তীর্ণ হওয়ার পথে রয়েছে । তৈরি পোশাক (RMG) খাতের গতিশীলতা এই দ্রুত রপ্তানি বৃদ্ধির প্রধান চালক ছিল ।
তবে এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি শক্তিশালী বাজার-বর্ধক প্রতিষ্ঠানগুলোর অনুপস্থিতি সত্ত্বেও ঘটেছে। দুর্নীতি সর্বব্যাপী ছিল এবং সরকারের সকল অঙ্গকে কলুষিত করেছিল । বাস্তবায়ন পর্যবেক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (IMED)-এর একটি সরকারি সমীক্ষায় দেখা গেছে, ৮০ শতাংশেরও বেশি প্রকল্প কর্মকর্তা উন্নয়ন কাজ বাস্তবায়নে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতার অভাবকে একটি প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন । এই অব্যবস্থাপনা এবং স্বচ্ছতার অভাব জনসাধারণের অসন্তোষের প্রধান উৎস ছিল।
এই অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ও সুশাসনের অভাবের সমান্তরাল সহাবস্থানকে ‘বাংলাদেশ প্যারাডক্স’ বলা হয় । এই প্যারাডক্সটি ইঙ্গিত করে যে, অর্থনৈতিক উন্নয়ন শক্তিশালী গণতান্ত্রিক সুশাসনের কারণে সম্ভব হয়নি, বরং রাজনৈতিক অভিজাতদের মধ্যে ‘রেন্ট-শেয়ারিং’-এর মাধ্যমে এক ধরনের দুর্বল “প্রবৃদ্ধি-বর্ধক শাসন” বিদ্যমান ছিল । যখন দুর্নীতি ও কর্তৃত্ববাদের এই ব্যবস্থাটি ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়—যা কোটা ব্যবস্থার বিরুদ্ধে যুব-নেতৃত্বাধীন আন্দোলন দ্বারা প্রমাণিত—তখনই আদর্শিক পরিবর্তনের সুযোগ তৈরি হয় । জবাবদিহিতার জন্য জনগণের আকাঙ্ক্ষা ছিল প্রবল, কিন্তু তা সম্পূর্ণরূপে ধর্মনিরপেক্ষ গণতন্ত্রের পক্ষে ছিল না। ইসলামপন্থীরা, মাদ্রাসার মতো সুসংগঠিত নেটওয়ার্কগুলোকে কাজে লাগিয়ে , দুর্নীতিগ্রস্ত ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর পরিচ্ছন্ন বিকল্প হিসেবে নিজেদের উপস্থাপন করে। তারা কার্যকরভাবে সুশাসনের ঘাটতিকে তাদের ধর্মীয় এজেন্ডা এগিয়ে নেওয়ার জন্য ব্যবহার করে ।
IV. ২০২৪ সালের সন্ধিক্ষণ: রাজনৈতিক রূপান্তর ও কাঠামোগত সংস্কার
A. ছাত্র আন্দোলন এবং গণতান্ত্রিক সুযোগের উন্মোচন
২০২৪ সালের জুলাই/আগস্ট মাসে ছাত্রনেতৃত্বাধীন সফল গণঅভ্যুত্থান, যার ফলস্বরূপ শেখ হাসিনার পদত্যাগ ঘটে, তা বাংলাদেশে একটি “অস্থায়ী গণতান্ত্রিক সুযোগের জানালা” তৈরি করে । এই আন্দোলনের তাৎক্ষণিক লক্ষ্য ছিল পূর্ববর্তী সরকারের সময়ের মানবাধিকার লঙ্ঘনের জন্য বিচারিক জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা এবং দুর্নীতি মোকাবেলা করা । এরপর ড. মুহাম্মদ ইউনূসের নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়।
B. অন্তর্বর্তী সরকার এবং অর্থনৈতিক ভঙ্গুরতা
অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতা গ্রহণের সময় তারল্য সংকট, বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ হ্রাস, উচ্চ মূল্যস্ফীতি এবং রমজানের সময় খাদ্য নিরাপত্তা নিশ্চিত করার মতো জরুরি অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হয় । সরকার রাজনৈতিক প্রতিশোধমূলক কাজগুলো পর্যালোচনা করে এবং রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি দিয়ে জবাবদিহিতার দিকে পদক্ষেপ নিয়েছে । তবে, অন্তর্বর্তী সরকার পূর্ববর্তী সরকারের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের ওপর হয়রানি ও হামলার ঘটনাগুলো পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ করতে পারেনি ।
C. সাংবিধানিক সংস্কার কমিশন (CRC) প্রস্তাবনা
অন্তর্বর্তী সরকার কর্তৃক গঠিত সাংবিধানিক সংস্কার কমিশন (CRC) ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে তার সুপারিশ জমা দেয়। এই প্রস্তাবনাগুলোর লক্ষ্য ছিল বাংলাদেশের কেন্দ্রীভূত ক্ষমতা কাঠামো ভেঙে দেওয়া এবং গণতান্ত্রিক জবাবদিহিতাকে শক্তিশালী করা ।
Table III: সাংবিধানিক সংস্কার কমিশনের (CRC) প্রধান প্রস্তাবনা (২০২৫)
| সংস্কার ক্ষেত্র | CRC প্রস্তাবনা | উদ্দেশ্য এবং প্রভাব | উৎস |
| নির্বাহী কাঠামো | সংসদীয় থেকে আধা-সংসদীয় মধ্যস্থতাযুক্ত ব্যবস্থায় পরিবর্তন। | শক্তিশালী প্রধানমন্ত্রীর ক্ষমতাকে বিকেন্দ্রীকরণ করা। | |
| মেয়াদ সীমা | রাষ্ট্রপতি এবং প্রধানমন্ত্রীর জন্য মেয়াদ সীমা প্রবর্তন। | দীর্ঘকাল ধরে ক্ষমতা ধরে রাখার মাধ্যমে কর্তৃত্ববাদী ক্ষমতা সঞ্চয় রোধ করা। | |
| তত্ত্বাবধান | জাতীয় সাংবিধানিক পরিষদ (NCC) গঠন। | সাংবিধানিক সংস্থাগুলোর নিয়োগ তদারকির জন্য একটি ‘মেটা-গ্যারান্টর’ প্রতিষ্ঠান হিসেবে কাজ করা। | |
| বিচার ব্যবস্থা | বিচারিক বিকেন্দ্রীকরণ। | রাজধানীতে বাইরেও ন্যায়বিচার প্রাপ্তি সহজ করা এবং আইনের শাসন শক্তিশালী করা। |
যদিও সিআরসি-এর প্রস্তাবনাগুলো অত্যন্ত গণতান্ত্রিক, তবে এই রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি ঝুঁকি বহন করে। অন্তর্বর্তী সরকার ‘অপরিহার্যতার নীতি’ (doctrine of necessity)-র উপর নির্ভর করে জরুরি পদক্ষেপ নিলেও , রাজনৈতিক রূপান্তরের চাপে আইনি প্রক্রিয়াকে পাশ কাটিয়ে যাওয়ার ঝুঁকি থাকে। এছাড়া, এই সংস্কার প্রক্রিয়ায় ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক দলগুলোকে (political stakeholders) প্রান্তিক করে রাখলে নতুন সংবিধান বা সংস্কারগুলোর ব্যাপক রাজনৈতিক বৈধতার অভাব হতে পারে । এই কারণে, সংস্কারের পদ্ধতি (নির্বাহী-নেতৃত্বাধীন প্রয়োজনীয়তা) তার গণতান্ত্রিক লক্ষ্যকে দুর্বল করে দেওয়ার ঝুঁকি তৈরি করে।
V. ইসলামপন্থীদের উত্থান: রাজনৈতিক শূন্যতার সুবিধা গ্রহণ
A. রাজনৈতিক ইসলামের পরিধি এবং কৌশলগত অবস্থান
বাংলাদেশে রাজনৈতিক ইসলামের আদর্শিক ভিত্তি অত্যন্ত বৈচিত্র্যময় । এর মধ্যে রয়েছে:
- নির্বাচনী/বাস্তববাদী (যেমন, জামায়াত-ই-ইসলামী): নির্বাচনী প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সমাজে ইসলামিক সামাজিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চায় এবং সংবিধানে “সর্বশক্তিমান আল্লাহর প্রতি পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস” ধারাটি পুনরুদ্ধারের দাবি জানায় ।
- আদর্শবাদী/অর্থোডক্স (যেমন, হেফাজত-ই-ইসলাম): কওমি মাদ্রাসাকেন্দ্রিক, গণ-ভিত্তিক সংগঠন, যারা ইসলামের ‘বাস্তব’ ব্যাখ্যার উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখতে চায় এবং দেশকে শরিয়াহ-ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে প্রতিষ্ঠার জন্য জনসমাগম করে ।
- নগর অভিজাত/খেলাফত প্রত্যাশী (যেমন, হিজবুত তাহরীর): শরিয়াহ আইনের অধীনে একটি বৈশ্বিক ইসলামিক খেলাফত প্রতিষ্ঠার লক্ষ্য রাখে; উচ্চ শিক্ষিত মধ্যবিত্ত নেতৃত্ব দ্বারা পরিচালিত এবং আন্তর্জাতিকভাবে সংযুক্ত ।
B. ২০২৪-পরবর্তী কৌশলগত সাফল্য এবং জনসমাবেশ
২০২৪ সালের অভ্যুত্থানের পর ইসলামপন্থী দলগুলো দ্রুত সক্রিয় হয়েছে। নিষিদ্ধ ঘোষিত হিজবুত তাহরীর ঢাকাতে একটি বিশাল সমাবেশ পরিচালনা করে (মার্চ ২০২৫), যেখানে তারা খেলাফত প্রতিষ্ঠার জন্য স্লোগান দেয় । এছাড়া তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাদের ছাত্র শাখা প্রতিষ্ঠা করে, যা রাষ্ট্রীয় নিষেধাজ্ঞা প্রয়োগের ক্ষমতা বা রাজনৈতিক ইচ্ছাশক্তির দুর্বলতা নির্দেশ করে।
হেফাজত-ই-ইসলামও ক্ষমতাশূন্যতার সুযোগ নেয় এবং ২০১৩ সালের ঘেরাও কর্মসূচির পর তাদের সবচেয়ে বড় সমাবেশ (২০২৫ সালের গ্র্যান্ড র্যালি) করে । তাদের দাবিগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: আহমদিয়া মুসলিম সম্প্রদায়কে আনুষ্ঠানিকভাবে অ-মুসলিম ঘোষণা করা , সঙ্গীত শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত সরকারি বিজ্ঞপ্তি বাতিল করা এবং ধর্মীয় প্রশিক্ষক নিয়োগের নির্দেশিকা তৈরি করা । অন্তর্বর্তী সরকার হেফাজতের এই ধর্মীয় দাবিগুলো বিবেচনা করছে বলেও জানা যায় ।
জামায়াতের ছাত্র শাখা (ইসলামী ছাত্র শিবির) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় (ডাকসু) এবং জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ছাত্র সংসদ নির্বাচনে বিজয় লাভ করে । বিশ্লেষকরা এই জয়কে ইসলামবাদের দিকে একটি মৌলিক আদর্শিক পরিবর্তন হিসেবে না দেখে, বরং জেনারেশন জেড-এর কৌশলগত ভোট হিসেবে ব্যাখ্যা করেন । শিক্ষার্থীরা ক্ষমতাসীন দলের (আওয়ামী লীগের ছাত্র শাখা) নিপীড়ক ছাত্র সংগঠনের বিরুদ্ধে সবচেয়ে কার্যকর বিরোধী শক্তি (শিবির/জামায়াত)-কে বেছে নিয়েছে। এটি প্রমাণ করে যে, যেখানে যুব সমাজ গণতন্ত্র ও জবাবদিহিতা চাইছে, সেখানে তাদের গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ইসলামপন্থীরা ব্যবহার করছে, যারা জনপ্রিয় দুর্নীতিবিরোধী ও অনাস্থা থেকে সুবিধা পাচ্ছে।
C. অন্তর্বর্তী সরকারের রাজনৈতিক হিসাব এবং আদর্শিক ছাড়
সমালোচকরা অন্তর্বর্তী প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস-এর বিরুদ্ধে নিষিদ্ধ এবং হার্ডলাইন ইসলামপন্থী গোষ্ঠীর সাথে আলোচনার মাধ্যমে “ধর্মকে রাজনৈতিক হাতিয়ার” হিসেবে ব্যবহার করার এবং সুযোগসন্ধানের অভিযোগ আনেন । অন্তর্বর্তী প্রশাসনের পক্ষ থেকে সংখ্যালঘুদের সুরক্ষা বা জঙ্গিবাদের লাগাম টেনে ধরার ক্ষেত্রে অনুভূত এই নীরবতাকে চরমপন্থীরা একটি ‘সবুজ সংকেত’ হিসেবে দেখে ।
ঐতিহ্যবাহী রাজনৈতিক ভিত্তি না থাকায়, অন্তর্বর্তী সরকার টিকে থাকার জন্য এবং সংস্কার এজেন্ডা বাস্তবায়নের জন্য বিস্তৃত সমর্থন চায় । এই মেরুকৃত রাষ্ট্রে, বহুত্ববাদ অর্জনের অর্থ হলো হেফাজতে ইসলামের মতো শক্তিশালী অ-ঐতিহ্যবাহী অভিনেতাদের সাথে বোঝাপড়া করা, যারা কওমি মাদ্রাসার মাধ্যমে যথেষ্ট সামাজিক প্রভাব রাখে । এই বোঝাপড়া একটি জটিল আপোষের জন্ম দেয়: সরকার তাৎক্ষণিক রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জন করে, কিন্তু বিনিময়ে রাষ্ট্রীয় নীতি, বিশেষ করে শিক্ষা এবং সংখ্যালঘুদের অধিকারের ক্ষেত্রে ধীর আদর্শিক অনুপ্রবেশের সুযোগ তৈরি হয়। এর ফলে রাষ্ট্রটি ধীরে ধীরে ব্যবহারকারীর আশঙ্কিত ইসলামপন্থী পথের দিকে ধাবিত হচ্ছে।
Table II: প্রধান ইসলামপন্থী অভিনেতাদের আদর্শিক অবস্থান এবং বর্তমান রাজনৈতিক প্রভাব (২০২৪-পরবর্তী)
| সংস্থা | আদর্শের ধরন | প্রধান দাবি (২০২৪-পরবর্তী) | প্রভাবের উৎস |
| হেফাজত-ই-ইসলাম | ঐতিহ্যবাহী/অর্থোডক্স (গণ-ভিত্তিক) | কাদিয়ানিদের অ-মুসলিম ঘোষণা; স্কুল পাঠ্যক্রমে ধর্মীয় নির্দেশনা। | ব্যাপক জনসমাবেশ ক্ষমতা (২০২৫ গ্র্যান্ড র্যালি); কওমি মাদ্রাসার উপর নিয়ন্ত্রণ । |
| হিজবুত তাহরীর | খেলাফত/বিপ্লবী (অভিজাত-ভিত্তিক) | শরিয়াহ আইনের ভিত্তিতে বৈশ্বিক ইসলামিক খেলাফত প্রতিষ্ঠা। | শিক্ষিত নগর যুবকদের লক্ষ্যবস্তু করা; আদর্শিক সংহতি; আন্তর্জাতিক সংযোগ । |
| জামায়াত-ই-ইসলামী | নির্বাচনী/বাস্তববাদী | মূলধারার রাজনীতিতে পুনঃপ্রবেশ; ক্যাম্পাসে কৌশলগত ভোট বিজয়। | অত্যন্ত সুসংগঠিত কাঠামো; সরকার-বিরোধী সেন্টিমেন্ট ব্যবহার (কৌশলগত ভোট) । |
VI. আইনি দ্বৈততা, বিচারিক স্থিতিস্থাপকতা এবং সংখ্যালঘুদের দুর্বলতা
A. আইনি ব্যবস্থার দ্বৈততা
বাংলাদেশের আনুষ্ঠানিক আইনি কাঠামোতে ধর্মনিরপেক্ষ ভিত্তি বজায় রয়েছে, যা বহুলাংশে ঔপনিবেশিক উত্তরাধিকার থেকে প্রাপ্ত । তবে, আইনি প্রেক্ষাপট ইসলামের নীতি দ্বারা প্রভাবিত, বিশেষত হানফি আইনতত্ত্ব (Hanafi jurisprudence) দ্বারা, যা মুসলমানদের ব্যক্তিগত বিষয়ে (যেমন, পারিবারিক আইনে) প্রয়োগ করা হয় । অনুচ্ছেদ ২ক (রাষ্ট্রধর্ম) এবং অনুচ্ছেদ ১২ (ধর্মনিরপেক্ষতা)-এর সহাবস্থান বিচার বিভাগকে একটি ঝুঁকিপূর্ণ ভারসাম্যমূলক কাজের মধ্যে ফেলে দেয় ।
B. বিচারিক চ্যালেঞ্জ এবং স্থিতিস্থাপকতা
ঐতিহাসিকভাবে, বিচার বিভাগ ধর্মনিরপেক্ষ মূল্যবোধ রক্ষায় তার স্বাধীনতা দেখিয়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বিচার বিভাগ অনানুষ্ঠানিক ফতোয়াগুলোর প্রভাব রোধ করতে সক্ষম হয়েছে, যা নারী ও সংখ্যালঘুদের উপর নিপীড়নের জন্য ব্যবহৃত হতো । সুপ্রিম কোর্ট ধর্মনিরপেক্ষ নীতিকে আরও জোরদার করতে একাধিক রায় দিয়েছে ।
C. ২০২৪-পরবর্তী সংখ্যালঘুদের চরম দুর্বলতা
২০২৪ সালের উত্থানের পরে সংখ্যালঘুদের, বিশেষত হিন্দুদের, রাজনৈতিকভাবে উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রতিশোধের সম্মুখীন হতে হয়েছে ।
বিচারিক ক্ষেত্রেও চরম ভঙ্গুরতা লক্ষ্য করা যায়, যেমন হিন্দু পুরোহিত কৃষ্ণ দাস প্রভুর মামলা । ২০২৪ সালের নভেম্বরে তাকে গ্রেফতার করা হয় এবং ২০২৫ সালের জানুয়ারিতে তার জামিন নামঞ্জুর করা হয়। ২০২৫ সালের মে মাসে সুপ্রিম কোর্ট হাইকোর্টের জামিনের আদেশে স্থগিতাদেশ দেয় ।
বিশ্লেষণে দেখা যায়, সাংবিধানিকভাবে ধর্মীয় বৈষম্য নিষিদ্ধ এবং সকল ধর্মের সমতার নিশ্চয়তা থাকা সত্ত্বেও , রাষ্ট্র রূপান্তরের পরে সংখ্যালঘুদের অধিকার ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে ব্যর্থ হয়েছে। এই ব্যর্থতা—যা রাজনৈতিকভাবে চার্জযুক্ত ধর্মীয় মামলায় বিচার বিভাগের জড়িয়ে পড়া এবং জঙ্গিবাদের প্রতি সরকারের নীরবতা—উভয় ক্ষেত্রেই প্রতীয়মান । এই পরিস্থিতি হার্ডলাইন গোষ্ঠীগুলোকে উৎসাহিত করে। এটি ইঙ্গিত দেয় যে রাষ্ট্র ধর্মনিরপেক্ষ সুরক্ষার অবস্থান থেকে সরে আসছে, যা আহমদিয়াদের অ-মুসলিম ঘোষণার মতো চরম আদর্শিক দাবিগুলোকে জোরদার করতে সাহায্য করছে । এই পরিবর্তন শরিয়াহ আইন সরাসরি বলবৎ করার চেয়েও বেশি, বরং রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে বিচারিক ও পুলিশি নিষ্ক্রিয়তার মাধ্যমে আদর্শিক পশ্চাদপসরণের ইঙ্গিত দেয়।
VII. সামাজিক সমতা: জনমত এবং রাষ্ট্রীয় পরিচয়ের ভবিষ্যত
A. ধর্মীয় প্রতিশ্রুতির গভীরতা
জনমত সমীক্ষা অনুসারে, বাংলাদেশ বিশ্বে অন্যতম ধর্মপরায়ণ রাষ্ট্র। প্রায় ৯৭ শতাংশ উত্তরদাতা ধর্মকে তাদের জীবনে ‘খুব গুরুত্বপূর্ণ’ মনে করেন । পাশাপাশি, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক (৪৫%) জনগণ ‘ধর্মীয় জাতীয়তাবাদী’ হওয়ার মাপকাঠি পূরণ করে , এবং দেশের মুসলমানদের জন্য শরিয়াহ আইনকে আনুষ্ঠানিক আইন হিসেবে দেখতে চান ।
B. ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি দ্বন্দ্বমূলক দৃষ্টিভঙ্গি
শিক্ষার্থীদের মধ্যে পরিচালিত গবেষণা একটি দ্বান্দ্বিক জনমত নির্দেশ করে। অর্ধেকেরও বেশি শিক্ষার্থী ধর্মনিরপেক্ষতাকে রাষ্ট্রের একটি নীতি হিসেবে পছন্দ করলেও, তারা এটিকে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট থেকে নেতিবাচকভাবে দেখে ।
ইতিহাসের আখ্যান নিয়েও সমাজে মতভেদ রয়েছে। কিছু গবেষণায় যুক্তি দেওয়া হয় যে, ধর্মনিরপেক্ষতা মুক্তিযুদ্ধের মূল ভিত্তি ছিল না, বরং এটি “উপর থেকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল” এবং যুদ্ধের মূল উদ্দেশ্য ছিল স্বায়ত্তশাসন ও গণতন্ত্র অর্জন । এই বিতর্কিত ঐতিহাসিক আখ্যানটি ইসলামপন্থীদের জন্য জনসমর্থন আদায়ে একটি গুরুত্বপূর্ণ হাতিয়ার হিসেবে কাজ করে।
C. আদর্শিক সমাবেশের ক্ষেত্রে মাদ্রাসা নেটওয়ার্কের ভূমিকা
কওমি মাদ্রাসাগুলো, যা সরকারের সরাসরি নজরদারির বাইরে পরিচালিত হয়, রাজনৈতিক সমাবেশের জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র । এই প্রতিষ্ঠানগুলো মূলত নিয়মিত মুসলমানদের আর্থিক অনুদানে চলে, ফলে তারা অর্থনৈতিকভাবেও স্বাধীন ।
এই মাদ্রাসাগুলোর সাথে যুক্ত আলেম সমাজ দেশে ইসলামের ‘বাস্তব’ ব্যাখ্যার উপর কর্তৃত্ব বজায় রাখে । তাদের সুস্পষ্ট লক্ষ্য হলো বাংলাদেশকে একটি শরিয়াহ-ভিত্তিক ইসলামী রাষ্ট্রে পরিণত করার জন্য জনগণকে সংগঠিত করা । কওমি মাদ্রাসা ব্যবস্থা রাজনৈতিক ইসলামের জন্য একটি অত্যন্ত স্থিতিস্থাপক এবং আদর্শিকভাবে ঐক্যবদ্ধ মানবসম্পদ নেটওয়ার্ক সরবরাহ করে। এই প্রাতিষ্ঠানিক রিজার্ভের কারণে হেফাজতের মতো হার্ডলাইন গোষ্ঠীগুলো ২০২৪ সালের রাজনৈতিক সংকটে দ্রুত গণসংগঠন করার ক্ষমতা অর্জন করে, যা বছরব্যাপী কর্তৃত্ববাদের কারণে দুর্বল হয়ে পড়া ধর্মনিরপেক্ষ দলগুলোর ছিল না।
VIII. বাংলাদেশের গতিপথের মূল্যায়ন
A. বিশ্লেষণের সংশ্লেষণ: একটি প্রতিযোগিতামূলক মিশ্র রাষ্ট্রীয় পরিচিতি
বাংলাদেশ ৫৪ বছর পর কোনো রৈখিক গণতান্ত্রিক পথে বা পূর্বনির্ধারিত ইসলামপন্থী পথে চলছে না। রাষ্ট্রটি প্রতিযোগিতামূলক মিশ্র রাষ্ট্রীয় পরিচিতি (Contested Hybridity) দ্বারা সংজ্ঞায়িত একটি অবস্থায় রয়েছে।
- সাংবিধানিক অস্থিরতা: রাষ্ট্রটি অভ্যন্তরীণভাবে অস্থিতিশীল দ্বৈততার (ধর্মনিরপেক্ষতা এবং রাষ্ট্রধর্ম) অধীনে কাজ করছে, যা রাজনৈতিক অভিনেতারা সুবিধা অনুযায়ী ব্যবহার করে ।
- গণতান্ত্রিক সুযোগ, আদর্শিক ঝুঁকি: ২০২৪ সালের সংকট জবাবদিহিতার উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করে একটি গণতান্ত্রিক সুযোগ এনেছিল, কিন্তু একইসাথে চাপা পড়ে থাকা আদর্শিক শক্তিগুলোকে উন্মুক্ত করে দিয়েছে। অভ্যুত্থানের মূল কারণ (দুর্নীতি, জবাবদিহিতার অভাব) রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এবং আদর্শিক আলোচনার তাৎক্ষণিক প্রয়োজনে সাময়িকভাবে চাপা পড়ে গেছে ।
- প্রভাব বিস্তারকারী শক্তি (The Dominant Vector): যদিও সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ গণতন্ত্র ও জবাবদিহিতাকে অগ্রাধিকার দিতে পারে, তবে ২০২৪-পরবর্তী শূন্যতায় সবচেয়ে সংগঠিত এবং আদর্শিকভাবে সুসংগঠিত অভিনেতারা হলো ইসলামপন্থীরা (হেফাজত, হিজবুত তাহরীর)। মূল কারণ হলো অন্তর্বর্তী সরকারের এই গোষ্ঠীগুলোকে রাজনৈতিকভাবে স্থান দেওয়ার সিদ্ধান্ত, যার মাধ্যমে স্বল্পমেয়াদী স্থিতিশীলতার জন্য দীর্ঘমেয়াদী আদর্শিক আপোষের ঝুঁকি নেওয়া হচ্ছে।
B. পূর্বাভাস পরিস্থিতি (স্বল্পমেয়াদী এবং দীর্ঘমেয়াদী)
১. সফল গণতান্ত্রিক প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ (কম সম্ভাবনা): যদি সিআরসি-এর প্রস্তাবনাগুলো সম্পূর্ণভাবে বাস্তবায়িত হয়, জবাবদিহিতা ও বিচার বিভাগের স্বাধীনতা শক্তিশালী হয়, এবং পরবর্তী নির্বাচিত সরকার সিদ্ধান্তমূলকভাবে সাংবিধানিক ধর্মনিরপেক্ষতা পুনঃপ্রতিষ্ঠা করে এবং চরমপন্থী সমাবেশ দমন করে। তবে এর জন্য তীব্র অর্থনৈতিক জরুরি অবস্থা এবং হার্ডলাইন চাপ কাটিয়ে ওঠা প্রয়োজন।
- ২. ত্বরান্বিত ইসলামীকরণ (মাঝারি সম্ভাবনা – বর্তমান প্রবণতা): অন্তর্বর্তী সরকার রক্ষণশীল ক্ষেত্রগুলোর চাপে আদর্শিক ছাড় দেয় (যেমন, শিক্ষায় পরিবর্তন, আহমদিয়াদের ঘোষণা)। সাংবিধানিক সংস্কার প্রক্রিয়া থেমে যায় বা ঐকমত্য ছাড়াই বাস্তবায়িত হয়। পরবর্তী নির্বাচিত সরকার (যা সম্ভবত দ্বি-দলীয় মেরুকরণে ফিরে যাবে) রাজনৈতিক লাভের জন্য ধর্মীয় জাতীয়তাবাদ ব্যবহার অব্যাহত রাখে, যা সাংবিধানিক পাঠ নির্বিশেষে রাষ্ট্রকে কার্যকরী ইসলামিক প্রজাতন্ত্রের দিকে ঠেলে দেবে।
- ৩. কর্তৃত্ববাদী স্থিতিস্থাপকতার প্রত্যাবর্তন (মাঝারি সম্ভাবনা): ব্যর্থ সাংবিধানিক সংস্কার গভীর প্রাতিষ্ঠানিক ভঙ্গুরতার দিকে নিয়ে যায়। অর্থনৈতিক সংকট আরও গভীর হয়। সামরিক বাহিনী বা একটি দৃঢ় কেন্দ্রীভূত নির্বাহী ক্ষমতা রাষ্ট্রকে স্থিতিশীল করার বা অর্থনৈতিক সংকট মোকাবিলার অজুহাতে ক্ষমতা পুনরায় দখল করে, যা ১৯৭৫-পরবর্তী কর্তৃত্ববাদী মডেলের পুনরাবৃত্তি ঘটাতে পারে।
C. নীতিনির্ধারণী প্রভাব ও সুপারিশসমূহ
বিশ্লেষণ থেকে উদ্ভূত তথ্য অনুযায়ী, রাষ্ট্রের বর্তমান পথকে গণতান্ত্রিক সুরক্ষার দিকে পরিচালিত করার জন্য নিম্নলিখিত পদক্ষেপগুলো জরুরি বলে বিবেচিত:
- শর্তাধীনতা ও জবাবদিহিতার ওপর গুরুত্ব: আন্তর্জাতিক সমর্থন (আইএমএফ, ইইউ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র) শুধু অর্থনৈতিক সংস্কারের ওপর নয়, বরং বিচারিক স্বাধীনতা এবং সকল সংখ্যালঘুর সাংবিধানিক অধিকার সুরক্ষায় বাস্তব অগ্রগতির ওপর কঠোরভাবে শর্তাধীন হওয়া উচিত । তহবিল বিতরণে অন্তর্বর্তী সরকারের বিচারবহির্ভূত বলপ্রয়োগ নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার কর্মদক্ষতা বিবেচনা করা উচিত ।
- সাংবিধানিক ঐকমত্যের সমর্থন: আন্তর্জাতিক অংশীদারদের সাংবিধানিক সংস্কার কমিশন প্রক্রিয়াকে প্রযুক্তিগত ও আর্থিক সহায়তা প্রদান করা উচিত, যেখানে সকল অংশীজন, বিশেষত প্রান্তিক ধর্মনিরপেক্ষ ও সংখ্যালঘু কণ্ঠস্বর, অন্তর্ভুক্ত হয়। এটি নিশ্চিত করবে যেন প্রস্তাবিত সংস্কারগুলো কেবল একটি চাপিয়ে দেওয়া নির্বাহী পদক্ষেপ হিসেবে বিবেচিত না হয় ।
- আদর্শিক প্রতিরোধ এবং সুশাসনকে লক্ষ্য করা: কেবল অর্থনৈতিক উন্নয়নে মনোনিবেশ না করে, অ-মাদ্রাসা শিক্ষাব্যবস্থার সংস্কার এবং সাংবিধানিক বহুত্ববাদকে উৎসাহিত করে এমন সুশীল সমাজ সংস্থাগুলোতে সম্পদ বিনিয়োগ করা উচিত। দীর্ঘমেয়াদে রাজনৈতিক ইসলামকে মোকাবিলার সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো সুশাসনের ঘাটতি (দুর্নীতি) দূর করা, কারণ ইসলামপন্থীরা ধর্মনিরপেক্ষ শাসনকে অকার্যকর প্রমাণ করার জন্য দুর্নীতিকেই প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে ।
বিশ্লেষণ ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র সমূহ: